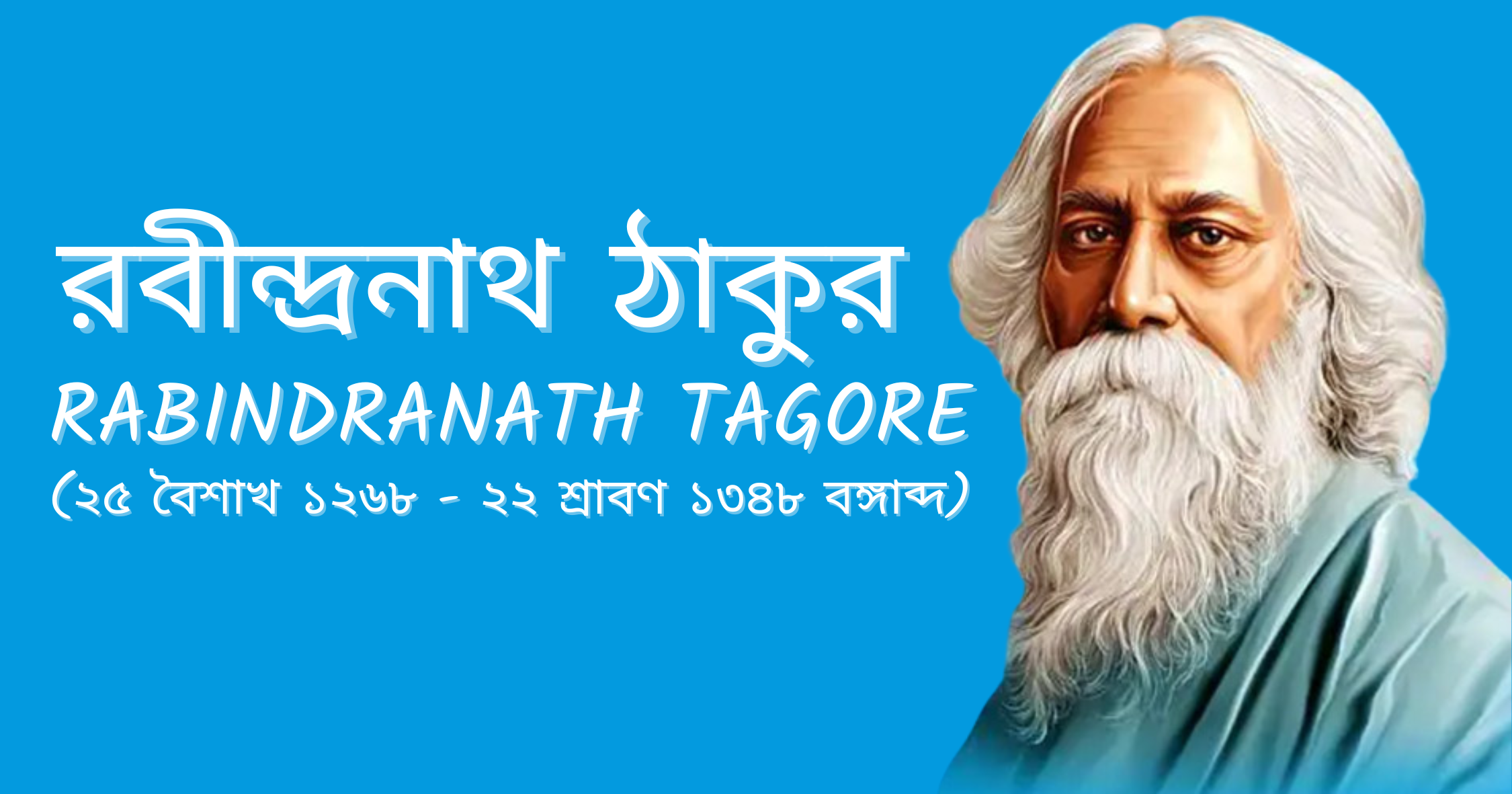রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore) (7 মে 1861 – 7 আগস্ট 1941; ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ – ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) ছিলেন একজন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সুরকার, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী এবং পি. তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে “গুরুদেব”, “কবিগুরু” এবং “বিশ্বকবি” উপাধি দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 52টি কবিতা সংকলন, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস এবং ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য সংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর পরপরই প্রকাশিত হয়েছিল। তার মোট ৯৫টি ছোটগল্প এবং ১৯১৫টি গান যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ এবং গীতবিতান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা রবীন্দ্র রচনাবলী শিরোনামে ৩২টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য আউটপুট ঊনিশ খণ্ডের চিঠিপত্র এবং চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি প্রায় দুই হাজার চিত্রকর্ম এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে, তিনি প্রথম অ-ইউরোপীয় এবং প্রথম এশীয় হয়েছিলেন যিনি তাঁর কবিতা সংকলন গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার এক ধনী ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম পিরালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার ঘাটভোগ ইউনিয়নের পিঠাভোগ গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক নিবাস অবস্থিত। শৈশবে তিনি ঐতিহ্যবাহী স্কুল শিক্ষা পাননি; তাঁর শিক্ষা বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষক দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর “অবিলাশ” কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথম ইংল্যান্ড সফর করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন। ১৮৯০ সাল থেকে, রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের জমিদারি এস্টেটে বসবাস শুরু করেন। ১৯০১ সালে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে একটি ব্রহ্মচারী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯০২ সালে তার স্ত্রী মারা যান। ১৯০৫ সালে তিনি বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৫ সালে, ব্রিটিশ সরকার তাকে “নাইট” উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্তু ১৯১৯ সালে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯২১ সালে, তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য শ্রীনিকেতন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার দীর্ঘ জীবনে, তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়েছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তিনি ১৯৪১ সালে কলকাতায় তাঁর পৈতৃক বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।
রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো চিন্তার গভীরতা, গীতিবাদ, চিত্রকল্প, আধ্যাত্মিকতা, ঐতিহ্য প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, মানবতাপ্রেম, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোমান্টিক সৌন্দর্য, ভাবের বৈচিত্র্য, ভাষা, ছন্দ ও শৈলী, বাস্তববাদ এবং প্রগতি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যও কাব্যিক। ভারতীয় শাস্ত্রীয় এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতি, সেইসাথে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং শৈল্পিক দর্শন, তার কাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি এবং জননীতি সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি গ্রামীণ উন্নয়ন এবং গ্রামে দরিদ্রদের শিক্ষাকে সামাজিক কল্যাণের উপায় হিসাবে তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি তিনি সামাজিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনে মানবজগৎকে ঈশ্বরের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবতার পরিবর্তে শ্রমিককে অর্থাৎ মানুষের ঈশ্বরকে পূজা করার কথা বলেছেন। তিনি সঙ্গীত ও নৃত্যকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি। তাঁর দুটি গান, “জানাজামান-আধিনায়ক জয় হে” এবং “আমার সোনার বাংলা” যথাক্রমে ভারত প্রজাতন্ত্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতটি শ্রীলঙ্কার জননী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।
পারিবারিক ইতিহাস
ঠাকুরদের আদি উপনাম ছিল কুশারী। কুশারীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশধর। দীন কুশারী মহারাজা ক্ষিতিশুর তাকে কুশ (বর্ধমান জেলায়) নামে একটি গ্রাম দেন এবং তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা হয়ে কুশারী নামে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশকের প্রথম খণ্ডে ঠাকুর পরিবারের বংশতালিকা দিয়েছেন, উল্লেখ করেছেন:
কুশারীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশধর; দীন মহারাজ ক্ষিতিশুরের কাছে কুশ (বর্ধমান জেলায়) নামক একটি গ্রাম খুঁজে পেয়ে তিনি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং কুশারী নামে পরিচিত হন। জগন্নাথ দীন কুশারীর অষ্টম বা দশম অবতার।
পরবর্তীতে কুশারীরা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে: যশোরের ঘাটভোগ-দামুড়হুদা থেকে ঢাকার কয়কীর্তন, বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে খুলনার পিঠাভোগ পর্যন্ত। পিঠাভোগের কুশারীরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধনী হয়ে ওঠে।
জীবন
প্রথম জীবন (১৮৬১–১৯০১)
শৈশব ও কৈশোর (১৮৬১ – ১৮৭৮)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ সোমবার কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ ধর্মীয় নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এবং তাঁর মা সারদাসুন্দরী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতা ও মাতার চতুর্দশ সন্তান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রবক্তা ছিল।
১৮৭৫ সালে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মা মারা যান। তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ বছরের বেশির ভাগ সময়ই কলকাতা থেকে দূরে থাকতেন, দেশে ঘুরে বেড়ানোর নেশায়। এভাবে ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে চাকরদের অনুশাসনে। শৈশবে, রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, নরমাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ স্কুলে কিছুকাল পড়াশোনা করেছিলেন। যাইহোক, স্কুল শিক্ষার প্রতি তার কোন আগ্রহ না থাকায় গৃহশিক্ষকের দ্বারা তাকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর নিজের বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশে বা বোলপুর ও পানিহাটির বাগানবাড়িতে ঘুরে বেড়াতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন ১৮৭৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ১২ বছর বয়সে পালিত হয়েছিল। তারপর তিনি কয়েক মাসের জন্য তার বাবার সাথে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তারা প্রথমে শান্তিনিকেতনে পৌঁছান। এরপর তিনি পাঞ্জাবের অমৃতসরে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন, শিখদের উপাসনা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ তার ছেলেকে নিয়ে পাঞ্জাবের ডালহৌসি শৈলশহরের কাছে (বর্তমানে ভারতের হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত) বাকরোটায় নিয়ে যান। বাকরোটা বাংলোতে বসে রবীন্দ্রনাথ তার বাবার কাছ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, জ্যোতির্বিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করতে শুরু করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনী, ধ্রুপদী সংস্কৃত কবিতা এবং কালিদাস ও উপনিষদের নাটক পড়তে উৎসাহিত করেন। ১৮৭৭ সালে, তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভারতী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো ছিল মাইকেল মধুসূদনের “মেঘনাদবধের কবিতার সমালোচনা”, ভানুসিংহ ঠাকুরের “পদাবলী” এবং “ভিখারিণী” ও “করুণা” নামে দুটি ছোটগল্প। তার মধ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলি রাধা ও কৃষ্ণ সম্পর্কে শ্লোক অনুকরণ করে “ভানুসিংহ” শৈলীতে লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প “ভিখারিণী” (১৮৭৭) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প। ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কবিকাহিনী’ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২) কবিতা সংকলনও রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা “নির্ঝরের স্বপ্নভাঙ্গা” এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
যৌবন (১৮৭৮-১৯০১)
১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আইন অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ডে যান। তিনি প্রথমে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৯ সালে, তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনে আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। তবে সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের কারণে তিনি পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়র এবং অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের রচনার সাথে পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে রিলিজিও মেডিসি, কোরিওলানাস এবং অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা পাঠ করেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় ইংল্যান্ডে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখতেন। এই নিবন্ধগুলি, তার বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনা সহ, “ইউরোপের তরুণ বাঙালি ভ্রমণের ডায়েরি” শিরোনামে সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮১ সালে, এই চিঠিগুলি ইউরোপীয় প্রবাসীদের চিঠি শিরোনামে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা এবং কথ্য ভাষায় লেখা প্রথম বই। অবশেষে, ১৮৮০ সালে, ইংল্যান্ডে প্রায় দেড় বছর কাটানোর পর, তিনি কোনও ডিগ্রি অর্জন না করেই বা আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু না করেই দেশে ফিরে আসেন।
১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর (২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৯০ বাংলা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুর পরিবারের অধস্তন কেরানি বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীকে বিয়ে করেন। তাদের বিবাহিত জীবনে ভবতারিণীকে মৃণালিনী দেবী (১৮৭৩-১৯০২) বলা হত। রবীন্দ্রনাথ এবং মৃণালিনীর পাঁচটি সন্তান ছিল: মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮), রথীন্দ্রনাথ (১৮৮৮-১৯৬১), রেণুকা (১৮৯১-১৯০৩), মীরা (অতসী) (১৮৯৪-১৯৬৯), এবং শমীন্দ্রনাথ (১৮৯৬-১৯০৭)। এদের মধ্যে রেণুকা ও শমীন্দ্রনাথ খুব অল্প বয়সে মারা যান।
১৮৯১ সাল থেকে, তার পিতার নির্দেশে, রবীন্দ্রনাথ নদীয়ার জমিদারদের (নদিয়ার অংশ যা বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা), পাবনা ও রাজশাহী এবং ওডিশা জেলাগুলির তত্ত্বাবধান শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ কর আদায় করতে এবং প্রজাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেতে শিলাইদহে “পদ্মা” নামক একটি বিলাসবহুল পারিবারিক বার্জে ভ্রমণ করতেন। গ্রামবাসীরাও তার সম্মানে উৎসব করত।
১৮৯০ সালে, রবীন্দ্রনাথের আরেকটি বিখ্যাত কবিতার সংকলন, মানসী প্রকাশিত হয়। তাঁর বিশ থেকে ত্রিশের দশকের মধ্যে আরও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ও গানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে প্রভাত সঙ্গীত, শেশসঙ্গিতা, রবিছায়া, কাদরী ও কোমল এবং অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কয়েকটি সেরা রচনা সাধনা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল, যা তিনি ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে সম্পাদনা করেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য জীবনের এই পর্বটি “সাধনা পর্ব” নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প সংকলনের প্রথম চুরাশিটি গল্পের অর্ধেক এই সময়ের রচনা। এসব গল্পে তিনি এঁকেছেন বাংলার গ্রামীণ জীবনের চলমান ও ব্যঙ্গাত্মক প্রতিকৃতি।
মধ্য জীবন (১৯০১–১৯৩২)
১৯০১ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার পরিবার বীরভূম জেলার বোলপুরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে শিলাইদহ ত্যাগ করেন। এখানে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম এবং ১৮৯১ সালে একটি ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের আম্রকুঞ্জ বাগানে একটি গ্রন্থাগার সহ “ব্রহ্ম বিদ্যালয়” বা “ব্রহ্মচর্যাশ্র” নামে একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ১৯০২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তার মেয়ে রেণুকা মারা যান; ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান; এবং ২৩ নভেম্বর, ১৯০৭ তারিখে, তার কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ মারা যান। এসবের মধ্যেই ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৬ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আধুনিক কৃষি ও পশুপালন শেখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান। ১৯০৭ সালে, রবীন্দ্রনাথও তার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃষি বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান।
এই সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে আর্থিক সংকট আরও তীব্র হয়। তদুপরি, রবীন্দ্রনাথকে তার ছেলে ও জামাইয়ের বিদেশে পড়াশোনার খরচও বহন করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ তার স্ত্রীর গয়না এবং পুরীর বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হন।
যাইহোক, ততদিনে কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বাংলা ও তার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০১ সালে নৈবেদ্য এবং ১৯০৬ সালে খেয়া কাব্য সংকলনের পরে, ১৯১০ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্য সংকলন গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে, সুইডিশ একাডেমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর কাব্য সংকলন গীতাঞ্জলি (ইংরেজি অনুবাদ, ১৯১২) এর ইংরেজি অনুবাদের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে। ১৯১৫ সালে, ব্রিটিশ সরকার তাকে ‘স্যার’ (নাইট) উপাধিতে ভূষিত করে। পরে, ১৯১৯ সালে, তিনি নৃশংস জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদে তার ব্রিটিশ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।
১৯২১ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমেরিকান কৃষি অর্থনীতিবিদ লিওনার্ড নাইট এলমহার্স্ট, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শান্তিনিকেতনের আরও কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের সহায়তায় শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুল গ্রামে “গ্রামীণ সংস্থা কেন্দ্র” নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ প্রতিরোধ করা, একটি সমবায় ব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, ভাল চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা এবং সাধারণভাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১৯২৩ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে “শ্রীনিকেতন” রাখেন। শ্রীনিকেতন ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতীক এবং প্রতিবাদমুক্ত স্বরাজ আন্দোলনের বিকল্প ব্যবস্থা। এটা লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে, বেশ কিছু দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ, দাতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীনিকেতনে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পাঠান।
১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা, গান এবং কবিতার একটি সিরিজে ভারতীয় সমাজে বর্ণপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।
শেষ জীবন (১৯৩২-১৯৪১)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের শেষ দশকে (১৯৩২-১৯৪১) মোট পঞ্চাশটি বই প্রকাশ করেন। এই সময়কালের তাঁর কবিতা সংকলনের মধ্যে তিনটি গদ্য কবিতা সংকলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), এবং শ্যামলী ও পত্রপুট (১৯৩৬)। জীবনের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল হল তাঁর বিভিন্ন গদ্য ও নৃত্যকর্ম, যার মধ্যে রয়েছে চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬; চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) নৃত্যের মাধ্যমে সম্পাদিত একটি কাব্যিক নাটক), শ্যামা (১৯৩৯), এবং চন্ডালিকা (১৯৩৯), একটি নৃত্য-নাট্য ত্রয়ী। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাস (দুই বন (১৯৩৩), মালঞ্চা (১৯৩৪) এবং চর অধ্যায় (১৯৩৪)) লিখেছেন। তাঁর বেশিরভাগ চিত্রকর্ম তাঁর জীবনের এই পর্যায়ে উত্পাদিত হয়েছিল। এ ছাড়াও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংকলন, বিশ্বপরিচয়, ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটিতে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলি সহজ বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব তাঁর কবিতায়ও স্পষ্ট। বিজ্ঞানীদের কেন্দ্র করে তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প তিনটি ছোট গল্প সংকলনে সংকলিত হয়েছে: সে (১৯৩৭), তিন সংঘি (১৯৪০), এবং গোলপোসাল্প (১৯৪১)।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবনের এই পর্যায়ে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। গান্ধীজি যখন ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ প্রদেশ বিহারে ভূমিকম্পে শত শত মানুষের মৃত্যুকে “ঈশ্বরের ক্রোধ” বলে অভিহিত করেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি এই ধরনের বক্তব্যকে অবৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে তার সমালোচনা করেছিলেন। কলকাতার সাধারণ মানুষের কঠিন আর্থিক পরিস্থিতি এবং ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক অবনতি তাকে বিশেষভাবে বিরক্ত করেছিল। গদ্যে লেখা ১০০ লাইনের কবিতায়ও তিনি এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।
তার জীবনের শেষ চার বছর ছিল অবিরাম শারীরিক অসুস্থতার সময়। এ সময় গুরুতর অসুস্থতার কারণে তিনি দুবার শয্যাশায়ী হন। ১৯৩৭ সালে, কবির অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং গুরুতর অবস্থায় ছিলেন। যদিও তিনি চাকরি থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন, কিন্তু ১৯৪০ সালে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি সুস্থ হতে পারেননি। এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মৃত্যুর সচেতনতাকে কেন্দ্র করে কিছু অবিস্মরণীয় শ্লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৃত্যুর সাত দিন আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃজনশীল ছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট জোড়াসাঁকোর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
বিশ্বভ্রমণ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট বারো বার পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে, তিনি পাঁচটি মহাদেশের ত্রিশটিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তার যৌবনে (১৮৭৮ এবং ১৮৯০ সালে) দুবার ইংল্যান্ড সফর করেছিলেন। ১৯১২ সালে, তিনি ব্যক্তিগত চিকিৎসার জন্য তৃতীয়বার ইংল্যান্ডে যান এবং ইয়েটস সহ বেশ কয়েকজন ইংরেজ কবি ও বুদ্ধিজীবীর কাছে তাঁর সদ্য রচিত কবিতা গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ পড়েন। তারাও কবিতা পড়ে মুগ্ধ। ইয়েটস নিজেই কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা লিখেছেন। এই সফরেই রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় ‘দ্বীনবন্ধু’ চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে। ১৯১৩ সালে, সুইডিশ একাডেমি তাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে। ১৯১৬-১৯১৭ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং সাম্রাজ্যবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি তাঁর জাতীয়তাবাদ (১৯১৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। যাইহোক, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উভয় দেশ সফরের সময় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে কবি আবার ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এই সফরে তাকে পশ্চিমা দেশগুলোতে স্বাগত জানানো হয়। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন সফর করেন। এরপর কবি চীন থেকে জাপান ভ্রমণ করেন এবং সেখানে জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তব্যও দেন। ১৯২৪ সালের শেষের দিকে, পেরুভিয়ান সরকারের আমন্ত্রণে, তিনি সেই দেশে যাওয়ার পথে আর্জেন্টিনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথেয়তায় তিন মাস অতিবাহিত করেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি পেরু সফর স্থগিত করেছেন। পেরু এবং মেক্সিকো সরকার পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীকে $১০০,০০০ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১৯২৬ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেনিটো মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালিতে যান। যদিও প্রথমে মুসোলিনির আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, কবি পরে জনসাধারণের কাছ থেকে তার একনায়কত্বের কথা জানার পর মুসোলিনির কর্মের সমালোচনা করেন। এতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভাঙ্গন দেখা দেয়। ভারতে ফেরার আগে রবীন্দ্রনাথ এরপর গ্রীস, তুরস্ক এবং মিশর ভ্রমণ করেন।
১৯২৭ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সহ চার সঙ্গী সহ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফর করেন। এই সময়ে তিনি বালি, জাভা, কুয়ালালামপুর, মালাক্কা, পেনাং, সিয়াম এবং সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সালে, কবি অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শেষবারের মতো ইংল্যান্ডে যান। এরপর তিনি ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। কবি ১৯৩২ সালে ইরাক ও পারস্য ভ্রমণ করেন। তারপর, ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সিংহল ভ্রমণ করেন। এটাই ছিল তার শেষ বিদেশ সফর।
রবীন্দ্রনাথ যে বইগুলিতে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলি হল: Letters from a European Exile (1881), Journal of a European Traveler (1891, 1893), Traveller to Japan (1919), Traveller (Journal of a Western Traveller and Letters of a Javanese Traveller, 1929), Letters from Sai (In31) এবং রাশিয়া (In319) রাস্তা (১৯৩৯)। তাঁর বিস্তৃত বিশ্ব ভ্রমণের ফলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক অরিজেন বার্গসন, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ফ্রস্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ, এইচজি ওয়েলস, রোমেন রোল্যান্ড এবং সিগমন্ড ফ্রয়েডের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মানবীয় পার্থক্য এবং জাতীয়তাবাদের প্রতি তার বিতৃষ্ণা তার জীবনের শেষ দিকে পারস্য, ইরাক এবং সিলন ভ্রমণের সময় তীব্র হয়েছিল। তাছাড়া তার বিশ্বভ্রমণ তাকে ভারতের বাইরেও তার লেখা উপস্থাপন করার এবং বহির্বিশ্বের সাথে রাজনৈতিক মতামত বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়।
সৃষ্টিকর্ম
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন কবি ছিলেন। আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি 52টি মৌলিক কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। তবে বাঙালি সমাজে তার জনপ্রিয়তা মূলত সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে তার মর্যাদার কারণে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুই হাজার গান লিখেছেন। কবিতা ও গান ছাড়াও তিনি ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটগল্প, ৩৬টি প্রবন্ধ ও গদ্য রচনা এবং ৩৮টি নাটক লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনা রবীন্দ্র রচনাবলী শিরোনামে ৩২টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর সমগ্র চিঠিপত্র উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যে নৃত্যশৈলী চালু করেছিলেন তা “রবীন্দ্র নৃত্য” নামে পরিচিত।
কবিতা
প্রথম জীবনে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) অনুসারী ছিলেন। বনফুল ও ভাংনাহৃদয় তাঁর তিনটি কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব স্পষ্ট। কাব্য সংকলন সন্ধ্যা সঙ্গীতের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন। সান্ধ্য সঙ্গীত, সকালের সঙ্গীত, ছবি ও গান এবং এই পর্বের কোমল ও কোমল কবিতার মূল বিষয় ছিল দুঃখ, আনন্দ, মৃত্যুর প্রেম এবং মানুষের হৃদয়ের মানবতা। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত তাঁর কাব্য সংকলন মানসী, এবং সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০) এবং ক্ষনিকা (১৯০০) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে রোমান্টিক চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) এবং গীতালি (১৯১৪) কাব্য সংকলনে এই চিন্তাটি মূর্ত হয়েছে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বলাকা (১৯১৬) আবারও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা প্রতিস্থাপন করে নশ্বর জীবনের প্রতি আগ্রহ দেখায়। পলটকা (১৯১৮) কবিতায় তিনি গল্প ও কবিতার আকারে নারী জীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার তার কাব্য সংকলন পূরবী (১৯২৫) এবং মহুয়া (১৯২৯) এ প্রেমকে সম্বোধন করেছেন। তখন চারটি গদ্য কবিতা প্রকাশিত হয়: পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), এবং শ্যামলী (১৯৩৬)। জীবনের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ কবিতার রূপ ও বিষয়বস্তু নিয়ে বেশ কিছু নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই সময়কালে, তিনি তার রোগসাথয্য (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জানদোনে (১৯৪১), এবং মরণোত্তর প্রকাশিত শেশ লেখা (১৯৪১) কবিতায় মৃত্যু ও ক্ষোভকে নতুন আলোয় অন্বেষণ করেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা “তোমার সৃষ্টির পথ” তার মৃত্যুর আট দিন আগে মৌখিকভাবে রচিত হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথের কবিতা মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব শ্লোক, উপনিষদ, কবিরের দোনবালি, লালনের বাউল গান এবং রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত শ্লোক দ্বারা প্রভাবিত। তবে প্রাচীন সাহিত্যের জটিলতার পরিবর্তে তিনি সহজ ও সুরেলা কাব্যশৈলী অবলম্বন করেন। আবার, ১৯৩০-এর দশকে কিছু পরীক্ষামূলক লেখার মাধ্যমে কবি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাস্তববাদের প্রাথমিক উত্থানের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীর বাইরে তাঁর সবচেয়ে পরিচিত কাব্য সংকলন হল গীতাঞ্জলি। এই বইটির জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। নোবেল ফাউন্ডেশন তার কবিতার সংগ্রহকে “কবিতার গভীরভাবে সংবেদনশীল, উজ্জ্বল এবং সুন্দর কাজ” বলে বর্ণনা করেছে।
ছোটগল্প
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল ছোটগল্পকার। হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার চাহিদা মেটাতে তিনি তাঁর গল্পগুলি লিখেছেন। এই গল্পগুলির উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের “সাধনা” সময়কাল (১৮৯১-৯৫) ছিল তাঁর সবচেয়ে সৃজনশীল পর্যায়। তাঁর ছোটগল্প সংকলনের প্রথম তিন খণ্ডের চুরাশিটি গল্পের অর্ধেক এই সময়ে লেখা। সংকলনের অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্র যুগে লেখা হয়েছিল (1914-1917; প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নামানুসারে)। তার উল্লেখযোগ্য কিছু গল্পের মধ্যে রয়েছে “কঙ্কল,” “নিশিতে,” “মণিহার,” “খুধিত পাষাণ,” “স্ত্রীর পত্র,” “নাস্তানীর,” “কাবুলিওয়ালা,” “হৈমন্তী,” “দেনাপাওনা,” “মুসলমানির গল্প” ইত্যাদি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প সংকলন লিপিকা, সে ও তিনসঙ্গীতে একটি নতুন শৈলীতে গল্প লিখেছেন।
রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই তাঁর গল্পগুলিতে তাঁর চারপাশের ঘটনা বা আধুনিক ধারণা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। কখনো কখনো তিনি তার গল্পে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোটগল্পের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র, নাটক এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। তার গল্পের কিছু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র রূপান্তর হল সত্যজিৎ রায়ের তিন কন্যা (“মনিহার”, “পোস্টমাস্টার” এবং “শম্পাথি” অবলম্বনে) এবং চারুলতা (“নাস্তানীর” অবলম্বনে), পরিচালিত তপন সিংহ, আথিয়া, কাবুলিওয়ালা এবং ক্ষুধিত পাষাণ, এবং স্ত্রীর চিঠি, পুরুপাত্রী ইত্যাদি।
উপন্যাস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট তেরোটি উপন্যাস লিখেছেন। এগুলি হল: বাউ-ঠাকুরানীর বাজার (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখেলি বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), প্রজাপতির নির্বাঁদ (১৯০৮), গোরা (১৯১০), ঘর বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), সমাচার (১৯২), সমাচার (১৯১৬), সমাচার (১৯১৯), (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪), এবং চর অধ্যায় (১৯৩৪)। দাদির হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ দুটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস লেখার প্রথম প্রচেষ্টা। এরপর থেকে তার ছোটগল্পের মতোই মাসিক পত্রিকার চাহিদা অনুযায়ী বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় তার উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।
‘ওখেক বালি’ উপন্যাসে সমসাময়িক সময়ের বিধবা জীবনের বিভিন্ন সমস্যার বর্ণনা রয়েছে। জটিল পারিবারিক সমস্যার উপর আলোকপাত করার জন্য “বোটস্ট্রাক” উপন্যাসটি পুনর্লিখন করা হয়েছে। গোরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি 19 শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু ও ব্রাহ্মসের মধ্যে সংঘর্ষ এবং সেই সময়ে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বর্ণনা করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে “ঘরের বাইরে” উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা আরও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার পরবর্তী উপন্যাস ‘যোগাযোগ’-এ। “চতুরঙ্গ” উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি “গল্প-শৈলীর উপন্যাস”। স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আসক্তির বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “দুই বোন” এবং “মালঞ্চা” উপন্যাস লিখেছেন। প্রথম উপন্যাসটি একটি রোম্যান্স, এবং দ্বিতীয়টি একটি ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চূড়ান্ত উপন্যাস চার আধ্যায় সমসাময়িক বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত একটি করুণ প্রেমের গল্প।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সত্যজিৎ রায়ের ঘর বেয়ারে এবং ঋতুপর্ণ ঘোষের অক্ষয় বালি।
প্রবন্ধ ও পত্রসাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও ইংরেজিতে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধগুলিতে, তিনি সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য তত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। সমাজচিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে সমাজ (১৯০৮) সংকলনে। বিভিন্ন সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ কালান্তর (১৯৩৭) সংকলনে সংকলিত হয়েছে। ধর্ম (১৯০৯) এবং শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় চিন্তা ও আধ্যাত্মিক বক্তৃতা সংগ্রহ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষ (১৯০৬), ইতিহাস (১৯৫৫) ইত্যাদি বইগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্যের গল্প (১৯৩৬), এবং সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩) গ্রন্থে সাহিত্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার দুটি বই যথাক্রমে প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭) এবং আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭) তে শাস্ত্রীয় ভারতীয় সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন। ফোকলোর (১৯০৭) বিষয়ক প্রবন্ধের ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলা লোকসাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), বাংলা ভাষা পারেকোটি (১৯৩৮) ইত্যাদি বইতে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি যথাক্রমে ছন্দ (১৯৩৬) এবং সঙ্গীতচিন্তা (১৯৬৬) গ্রন্থে ছন্দ ও সঙ্গীত বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধের সিরিজ, শিক্ষা (১৯০৮) এ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ (১৯১৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উগ্র জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণ ও বিরোধিতা করেছেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে তিনি দর্শনের উপর যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা দ্য রিলিজিয়ন অফ ম্যান (১৯৩০) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। তাঁর শেষ প্রবন্ধের বই ছিল দ্য ক্রাইসিস অফ সিভিলাইজেশন (১৯৪১), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি জন্মদিনের ঠিকানা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭) নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে জীবনস্মৃতি (১৯১২), চেলেবেলা (১৯৪০), এবং আত্মপরিচয় (১৯৪৩)।
রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য আউটপুট আজ পর্যন্ত উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী (তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লেখা), ভানুসিংহের পাত্রাবলি (রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়কে লেখা) এবং পোঠে ও পথের পাঁধন (নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা) এই তিনটি গ্রন্থ হল রবিনাথের তিনটি উল্লেখযোগ্য পত্র সংগ্রহ।
নাট্যসাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। ষোল বছর বয়সে, বড় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত হঠাৎ নবাব (মলিয়েরের লা বুর্জোয়া অবলম্বনে) নাটকে এবং পরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের একই পরিবারের দ্বারা রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অলিকবাবুর নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম গীতিনাটক, বাল্মীকি প্রতিভা, ১৮৮১ সালে পরিবেশিত হয়েছিল। এই নাটকে তিনি ঋষি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮২ সালে, রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে কালমৃগয়া নামে আরেকটি গানের নাটক রচনা করেন। এ নাটকে তিনি অন্ধমুনি চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
গীতিনাট্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু কাব্য রচনা করেন। শেক্সপিয়রীয় পেন্টামিটার স্টাইলে রচিত তাঁর দ্য কিং অ্যান্ড দ্য কুইন (১৮৮৯) এবং দ্য অ্যাবন্ডনমেন্ট (১৮৯০) নাটকগুলি বহুবার পাবলিক মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছিল এবং তিনি নিজেও এই নাটকগুলিতে অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথ রাজা ও রানী নাটকে বিক্রমদেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি বিসর্জন নাটকটি দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেন। ১৮৯০ সালের প্রযোজনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং ১৯২৩ সালের প্রযোজনায় প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ তরুণ জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাব্যনাট্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) এবং মালিনী (১৮৯৬)।
কাব্য নাটকের পর রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়কালে, গোরায়া গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের ডায়েরি (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৯), এবং ব্যাংগৌতুক (১৯০৭) প্রকাশিত হয়। বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে তিনি রবীন্দ্রনাথ কেদার চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯২৬ সালে, তিনি প্রজাপতির অসমাপ্ত উপন্যাসটিকে চিরকুমার সভা নামে একটি নাটকে রূপান্তরিত করেন।
১৯০৮ সাল থেকে, রবীন্দ্রনাথ রূপক ও প্রতীকী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নাটক লিখতে শুরু করেন। তিনি ইতিমধ্যে তার নেচার’স রিভেঞ্জ (১৮৮৪) নাটকে কিছু রূপক ও প্রতীকী রূপ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ১৯০৮ সাল থেকে তিনি এই রীতিতে একের পর এক নাটক লিখতে শুরু করেন। এই নাটকগুলো হলো: শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), তাসের দেশ (১৯৩৩), কালের যাত্রা (১৯৩২) এই সময়ে রবীণনাথ ও রবীণনাথের মঞ্চায়নে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। ছাত্রদের সঙ্গে অভিনয় দল গঠন. মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে ছাত্রদের নিয়ে নাটক করতেন। এই সব নাটকে রবীন্দ্রনাথ একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ১৯১১ সালের শারদোৎসব নাটকে একজন সন্ন্যাসীর যৌথ ভূমিকা এবং রাজা নাটকে একজন রাজা ও পিতামহের যৌথ ভূমিকা; তিনি ১৯১৪ সালে অচলায়তন নাটকে আদিনপুন্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন; ১৯১৫ সালে ফাল্গুনী নাটকে তিনি অন্ধ বাউল চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯১৭ সালে ডাকঘর নাটকে তিনি দাদা, প্রহরী ও বাউলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নাটক লেখার পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ের মধ্যে ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য নতুন নামে পুরানো নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। শারদোৎসব নাটকটি রীনাশোদ (১৯২১), রাজা অরূপরতন (১৯২০), অচলায়তন গুরু (১৯১৮), গোরায়া গলদ শেষরক্ষা (১৯২৮), রাজা ও রানি তপতী (১৯২৯), এবং পর্যচিত্ত পরিত্রান (১৯২৯) হয়েছিলেন।
১৯২৬ সালে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটির পূজা নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি নাচ ও গানের প্রচলন করেন। এই ধারাটি তার জীবনের শেষ পর্যায়ে “নৃত্যনাট্য” নামে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। নৃত্যনাট্য নাতির পূজার পর রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন শাপামোচন (১৯৩১), তাসের দেশ (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামা (১৯৩৯)। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা এটিও প্রথম মঞ্চস্থ করেছিল।
সংগীত ও নৃত্যকলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৫টি গান রচনা করেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাংলা লোকসংগীত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীত এই তিনটি ধারাকে শুষে নিয়ে তিনি একটি অনন্য সঙ্গীত শৈলী তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করেছেন। রবীন্দ্র পণ্ডিত সুকুমার সেন রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনার ইতিহাসে চারটি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট গানের উপর ভিত্তি করে গান রচনা শুরু করেন। দ্বিতীয় পর্বে (১৮৮৪-১৯০০), রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ গান ও কীর্তনের উদাহরণ অনুসরণ করে নিজের সুর দিয়ে গান রচনা শুরু করেন। ১৯ শতকের বিশিষ্ট সুরকার যেমন মধুকন, রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক প্রমুখের প্রভাব এই পর্বের রবীন্দ্রসঙ্গীতেও স্পষ্ট। এরপর থেকে, তিনি নিজের রচিত কবিতার সুর সেট করে গান রচনা করতে শুরু করেন। ১৯০০ সালে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করার পর থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনার তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সুর ও চেতনাকে তাঁর নিজের গানে যুক্ত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথের গান রচনার চতুর্থ পর্ব শুরু হয়। এই সময়ের কবির গানগুলি নতুন কৌশল ব্যবহার এবং অনন্য এবং কঠিন সুর সৃষ্টি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাঁর রচিত সমস্ত গান গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই বইটি “উপাসনা,” “প্রেম,” “প্রকৃতি,” “স্বদেশ,” “আনুষ্ঠানিক” এবং “বিবিধ” বিভাগের অধীনে মোট ১৫০০টি গান সংকলন করেছে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থে বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যনাট্য, নাটক, কবিতা সংকলন এবং অন্যান্য সংকলন থেকে অনেক গান সংকলিত হয়। বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া গীতিনাট্য, এবং চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা এবং শ্যামা সম্পূর্ণরূপে গানের বিন্যাসে লেখা, ইউরোপীয় অপেরার আদলে তৈরি।
রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাংলায় শিক্ষিত পরিবারে নৃত্যচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী পাঠ্যক্রমে সঙ্গীত এবং চিত্রকলার সাথে নৃত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলীর সমন্বয়ে একটি নতুন শৈলী প্রবর্তন করেন। এই শৈলীটি “রবীন্দ্র নৃত্য” নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ও নৃত্যনাট্যে গানের পাশাপাশি নৃত্যও অপরিহার্য। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্কর দ্বারা আধুনিক ভারতীয় নৃত্যশৈলী প্রবর্তনের পিছনেও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শিক্ষাচিন্তা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন খুবই জটিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করেছিলেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত কাব্য সংকলন মানসীর কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে। হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার প্রমাণ এবং পরে প্রকাশিত তথ্য প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথ শুধু গদর ষড়যন্ত্র সম্পর্কেই জানতেন না বরং ষড়যন্ত্রে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তেরৌচি মাসাতাকি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওকুমা শিগেনোবুর সাহায্যও চেয়েছিলেন। আবার, ১৯২৫ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, এটিকে “চরকা সংস্কৃতি” বলে উপহাস করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল, তার দৃষ্টিতে, “আমাদের সামাজিক সমস্যার রাজনৈতিক লক্ষণ।” তাই তিনি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সাধারণ জনগণের জন্য আত্মনির্ভরশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ওপর অধিক জোর দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবাসীকে অন্ধ বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে নিরলস, প্রগতিশীল শিক্ষার পথ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ধরনের আদর্শ অনেককে বিরক্ত করে। ১৯১৬ সালের শেষের দিকে, একদল চরমপন্থী বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সান ফ্রান্সিসকোতে একটি হোটেলে থাকার সময় তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি তার নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লর্ড চেমসফোর্ডকে লিখেছিলেন: “আমার প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর নীরব কষ্টের প্রকাশ।” রবীন্দ্রনাথের “চিত্ত যেঠা ভৈষ্যূন্য” এবং “একলা চলো রে” রাজনৈতিক রচনা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। “একলা চলো রে” গানটি গান্ধীজীর খুব প্রিয় ছিল। যদিও মহাত্মা গান্ধীর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক তিক্ত ছিল, তবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে গান্ধীজি এবং আম্বেদকরের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দেয় তা সমাধানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফলে গান্ধীও তার অনশন প্রত্যাহার করে নেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্প “তোতা-কাহিনী” তে স্কুলের রোট লার্নিংকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে দেশের ছাত্রসমাজকে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো শুকনো জ্ঞান গিলে মেধা মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ১১ অক্টোবর, ১৯১৭ সালে, ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা ভ্রমণের সময়, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে অপ্রচলিতভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। এই সময়েই কবি শান্তিনিকেতন আশ্রমকে দেশ ও ভূগোলের সীমানা ছাড়িয়ে ভারত ও বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি বৈশ্বিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও করেছিলেন। তাঁর স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর, যাকে বলা হয় বিশ্বভারতী, ২২ অক্টোবর, ১৯১৮-এ স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর, ২২ ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে, এই স্কুলটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। বিশ্বভারতীতে, কবি ব্রহ্মচর্য এবং গুরুত্বের ঐতিহ্যগত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেন। তিনি এই স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি নোবেল পুরস্কার হিসেবে যে অর্থ পেয়েছেন তা এই বিদ্যালয়ের প্রশাসনকে দান করেছেন। তিনি নিজে শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সকালে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ক্লাস নিতেন এবং বিকেল ও সন্ধ্যায় তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখতেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে, তিনি স্কুলের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বেশ কয়েকবার ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন।
প্রভাব
বিংশ শতাব্দীর বাঙালি সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব ব্যাপক। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিক অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একজন “হিমালয় ব্যক্তিত্ব” এবং “গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক এবং বহুমুখী সমসাময়িক দার্শনিক” হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৩২ খণ্ডের রচনা, রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধন হিসেবে বিবেচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে “ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি” হিসাবেও বর্ণনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী “পঞ্চীশে বৈশাখ” এবং তার মৃত্যুবার্ষিকী “বৈশে শ্রাবণ” আজও বাঙালি সমাজে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে প্রচুর ভিড় জমায়। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সূচিত ধর্মীয় ও ঋতু উৎসবের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানানোর ঐতিহ্য অব্যাহত রয়েছে। তদুপরি, বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার বা রবীন্দ্র রচনা আবৃত্তি করার প্রথা দীর্ঘদিন ধরে বজায় রয়েছে। এগুলি ছাড়াও কবির সম্মানে অন্যান্য বিশেষ ও অনন্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়, আরবানাতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ‘রবীন্দ্র উৎসব’, কলকাতা-শান্তিনিকেতনের ‘রবীন্দ্র পাঠপরিক্রমা’ তীর্থযাত্রা ইত্যাদি।
তাঁর জীবদ্দশায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের একটি প্রগতিশীল সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডার্টিংটন হল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি অনেক জাপানি লেখককে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে ইয়াসুনারি কাওয়াবাটা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বই ইংরেজি, ডাচ, জার্মান এবং স্প্যানিশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। চেক ইন্ডোলজিস্ট ভিনসেঞ্জ লেনচি সহ তার কাজগুলি বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি লেখক আন্দ্রে গিদে, রাশিয়ান কবি আনা আখমাতোভা, তুরস্কের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত একিবেট এবং আমেরিকান ঔপন্যাসিক জোনাহ গ্যাল সহ অনেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় এবং প্রশংসিত হয়েছিল। যাইহোক, বিভিন্ন বিতর্কের কারণে 1920 এর দশকের শেষের দিকে জাপান এবং উত্তর আমেরিকায় তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। সময়ের সাথে সাথে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার বাইরে “প্রায় বিলুপ্ত” হন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে স্প্যানিশ-ভাষী লেখকদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে চিলির লেখক পাবলো নেরুদা এবং গ্যাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল, মেক্সিকান লেখক অক্টাভিও পাজ এবং স্প্যানিশ লেখক হোসে ওর্তেগা ওয়াই গাসেট, থেনোবিয়া ক্যাম্পরুবি আইমার এবং জুয়ান রামন জিমেনেজ। ১৯১৪ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে, হিমেনেথ-কমপ্রুবি দম্পতি রবীন্দ্রনাথের বাইশটি বই ইংরেজি থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তারা দ্য ক্রিসেন্ট মুন (শিশু ভোলানাথ) সহ রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি কাজের বিশদ পর্যালোচনা এবং স্প্যানিশ সংস্করণও প্রকাশ করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সময়েই হিমেনেথ “নগ্ন কবিতা” নামে একটি বিশেষ সাহিত্য শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন।
অনেক পাশ্চাত্য লেখক ও সাহিত্য সমালোচক যারা রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা কবিতা পড়েননি তারাও রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বকে উড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রাহাম গ্রিন সন্দেহের সাথে মন্তব্য করেছিলেন, “ইয়েটস ছাড়া কেউই রবীন্দ্রনাথের লেখাকে গুরুত্বের সাথে নেয় না।” সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার কিছু প্রাচীন ল্যাটিন আমেরিকার খন্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। সালমান রুশদি নিকারাগুয়া সফরের সময় এমন কিছু উদাহরণ দেখে অবাক হয়েছিলেন।